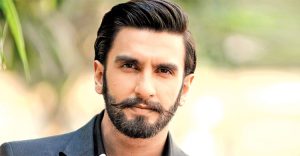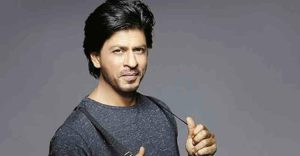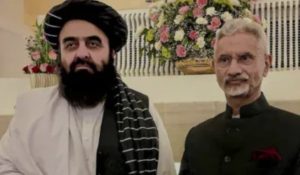৭১-এর ১৫ আগস্ট রাতে চট্টগ্রাম বন্দরে কেয়ামত নেমে এসেছিলো। সে রাতে মুক্তিবাহিনীর নৌ কমান্ডোরা বন্দরে অবস্থানরত পাকিস্তানি জাহাজগুলিতে মাইন লাগিয়েছিলো এবং বিকট শব্দে সেগুলি একের পর এক যখন বিস্ফোরিত হচ্ছিলো, তখন চট্টগ্রাম বন্দরে খÐ প্রলয় সৃষ্টি হয়েছিলো। বিস্ফোরণের ধাক্কা এবং প্রচÐ আওয়াজে গোটা চট্টগ্রাম শহর এবং আশেপাশের এলাকা ভ‚মিকম্পের ন্যায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিলো। আন্তর্জাতিক শিপিং লাইন এবং বীমা কোম্পানির মাধ্যমে বিশ্বময়, এমনকি জাতিসংঘেও ধ্বংসের বার্তা পৌঁছে গিয়েছিলো। এতে ১০টি টার্গেট সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস বা নিমজ্জিত হয়। এগুলো ছিল জাহাজ, গানবোট, বার্জ ও পন্টুন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম এ ঘটনা ফলাও করে প্রচার করে।
জ্যাকপটের উদ্দেশ্য ছিলো পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবল ভেঙে দেয়া এবং পাকিস্তানে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ চলছে সেটা প্রমাণ করা। এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলো। মাত্র ১৯ জুলাই বেলুনিয়ার চাঁদগাজীতে পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিবাহিনীর সর্বশেষ প্রতিরোধ যুদ্ধ জিততে না জিততেই এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে মুক্তিবাহিনী ব্যাপক বিধ্বংসী আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবল ভেঙে চুর চুর করে দিয়েছিলো। এ কারণে মুক্তিযুদ্ধে অপারেশন জ্যাকপটের গুরুত্ব অপরিসীম। এই একটি অভিযান মুক্তিযুদ্ধকে অন্য উচ্চতায় উন্নীত করেছিলো। সুতরাং অপারেশন জ্যাকপটে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা আমাদের জাতীয় বীর। অপারেশন জ্যাকপটের অন্যতম কমান্ডার ছিলেন জনাব ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক। সে হিসেবে তিনিও একজন জাতীয় বীর। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ রণনৈপুণ্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করায় তিনি বীর প্রতীক খেতাবে ভ‚ষিত হন। জাতীয় বীর থেকে ২০২৪ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি। এ এক অনন্য গৌরব। ফারুক-ই-আজমের পক্ষেই শুধু একের পর এক গৌরবের রেকর্ড স্থাপন করা সম্ভব। তাঁর জীবনে নানা ব্যক্তিক্রমী ঘটনা ঘটে, যা’ তাঁকে একজন অসাধারণ মানুষের মহিমা দান করেছে। যেমন মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে তিনি খুলনায় কর্মরত ছিলেন। ২৫ মার্চ পাক বাহিনীর পাশবিক নরমেধযজ্ঞ, ধ্বংস, আগুন ও কামান-ট্যাংকের গর্জনে তাঁর প্রিয় মাতৃভ‚মির শ্যামল, সবুজ কানন যখন হায়েনা কবলিত হয়, তখনো তিনি খুলনায়; সর্বনাশের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার জন্য বিপন্ন মাতার আকুল আর্তি মর্মে পৌঁছে বুকফাটা কান্নায় তাঁর অন্তর আর্তনাদ করে উঠে, ক্রোধে আরক্তিম সন্তান প্রতিশোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেও তাঁর কিছুই করার উপায় ছিলো না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানের কথা শুনে মুক্তিযুদ্ধের যোগদানের জন্য তিনি লাফিয়ে উঠেছিলেন। পরে বাঙালি সামরিক অফিসার মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণায় যুদ্ধে যোগদানের জন্য তিনি আরো উদগ্রীব হয়ে উঠেন।
খুলনা থেকে চট্টগ্রাম দুস্তর পারাবার লঙ্ঘিতে ছুটে উঠে গেলেন এক জাহাজে এবং অনেক জল ও স্থলপথ অতিক্রম করে নীড়ে ফিরে এসেছিলেন কাটিরহাটের দুলাল। অধুনা হাটহাজারী নামে পরিচিত হোসেন শাহী আমলের রাজধানী ফতেয়াবাদ মুলুকের নাজিরহাট ঘেঁষা হালদা কুলের কাটিরহাট পল্লীর এমন এক পাড়ায় ফারুক-ই-আজমের বসতি, ফারুকের কথায় তাঁর চাচা-ভাইপো মিলে সরাসরি মুক্তিযোদ্ধা ১০ জন। ফারুকের তর সইছে না ট্রেনিংয়ের জন্য ভারতে যেতে, ক্রোধে হাত পা নিশপিশ করছে; ছোটবেলা থেকেই দুরন্ত ফারুক।
সব মুক্তিযোদ্ধাই জীবন দেয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন; কিন্তু ফারুক নৌ কমান্ডো বাহিনী নামে যে বাহিনীতে নাম লেখালেন, সেটি আবার নামেও ‘সুইসাইড মিশন’, সই করতে হলো ‘আত্মঘাতী আক্রমণ’ ফরমে।
কমান্ডো কম নয়, কিন্তু কমান্ডার করগণ্য। সেখানেও ফারুক-ই-আজম একজন কমান্ডার। নদী মাতৃক বাংলাদেশের পানির হাঙর-কুমির হয়ে গেলেন তাঁরা। তাঁদের লিমপেট মাইন যখন কামড় দেয়, হাঙর-কুমিরের চেয়েও ধারালো দাঁত ফালাফালা, ছিন্নভিন্ন করে ফেলে শত্রæর জাহাজ, স্টিমার, টাগ। জলের নিচে ফারুক এমন হাঙর-কুমির হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর অসাধারণ শৌর্য বীর্যের স্বীকৃতি পেলেন বীর প্রতীক খেতাবে। আরো কেউ কেউ পেয়েছেন সেটা, সবাই নয়। যেমন এ ডবিøউ চৌধুরী বীর উত্তম বীর বিক্রম, শাহ আলম বীর উত্তম, মাজহারউল্লাহ বীর উত্তম।
যুদ্ধে বিজয়ী ফারুক; পরাধীনতার রাহুগ্রাস থেকে দেশমাতাকে মুক্ত করতে পেরে সে কী আনন্দ তাঁর। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর স্বদেশে বিজয়ের চেতনা ফিকে হয়ে আসতে দেখে ব্যাথাহত, ক্ষুব্ধ ফারুক ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন বিজয় মেলা – এক নতুন কনসেপ্ট। একা করেননি, আরো ছিলেন সঙ্গে, সাংবাদিক আজিজুল ইসলাম ভ‚ঁইয়া ও আখতার-উন-নবী, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল মান্নান, কবি ও সাংবাদিক আবুল মোমেন, আইনজীবী অ্যাডভোকেট রাণা দাশগুপ্ত।
ফারুকের মধ্যে আছে এক বাউল মন। ছোটবেলায় গ্রামে খালবিল দাপিয়ে বেড়ানোর সময় শুনতে পেতেন পানাভর্তি ডোবায় ডাহুকের ডাক, পানকৌড়ির আর্তরব। বাঙালি মাত্রই কবি, এই লোকপ্রসিদ্ধি সত্য হলে শিল্পী হতেও বাধা নেই তার। বাংলার চাষী পাটি বোনে, নকশী কাঁথায় নক্সশা আঁকে গৃহবধূ, বাঁশ ও বেতের লাই, কুলা, ডালা, চাই তৈরি করে কারুশিল্পী, তাঁতের কাপড় বানায় তাঁতী ও জোলা, কলমীলতা, পদ্মপাতা, শাপলা শালুকের দেশগ্রামে, হাটে-বাটে-ঘাটে, তেপান্তরের মাঠে রাখাল বালকের বাঁশির সুরে, বাংলার বিস্তৃত নদীতে মাঝির ভাটিয়ালী, পল্লীগীতির সুরে কোন বিরহী হৃদয়ের কান্না গুমরে গুমরে মরে। আউল-বাউলের উদাস চাহনি কী খোঁজে সুদূরের পানে। ফারুক-ই-আজমের শিল্পীসত্তার গভীর থেকে উঠে আসে বয়ন-বুনন শিল্পের তাড়না। গ্রামে দেখা আবহমান বাংলার কুটির শিল্প ও হস্তশিল্পের বাঁশ, বেতের সামগ্রী, তাঁত, চরকা এবং নারীর পেলব হস্তে বোনা রমণীয় সেলোয়ার, কামিজ, পিনন, পাঞ্জাবী ইত্যাদির বাহারির বুনন ঘাই মারে ফারুক-ই-আজমের অন্তরের গহীন দেশে। তিনি বাংলার লুপ্তপ্রায় লোকজ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য চট্টগ্রাম শহরের মেহেদীবাগে ‘রমণীয়া’ নামে এক হস্তশিল্পের মনোহর প্রদর্শনী খুলে বসেন। ‘রমণীয়া’ চট্টগ্রামের প্রথম ফ্যাশন বুটিক। ফ্যাশন প্রতিযোগিতার জন্য পোশাক ডিজাইন করে তিনি শতাধিকবার জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত হন। ১৯৮৩ সাল থেকে তিনি তৎকালীন সাপ্তাহিক বিচিত্রার সঙ্গে দেশীয় কাপড় এবং পোশাকের মান উন্নয়নের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁতিদের সঙ্গে কাজ করেন।
ফারুক-ই-আজম চট্টগ্রাম শহরের সমস্ত প্রগতিশীল কর্মকাÐ, নাগরিক উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট থেকে জনমত গঠন ও চিন্তার উপরিকাঠামোতে অবদান রাখেন। প্রাকৃতিকভাবে মনোরম নগর চট্টগ্রাম ভ‚মিপুত্রদের আগ্রাসী ভূমিক্ষুধা, যথেচ্ছাচার, খামখেয়ালীপনা এবং অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে চট্টগ্রাম যে শ্রীহীন হয়ে বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে, সেটা দেখে অসহায় নগরবাসী হাত পা গুটিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকলেও প্রকৌশলী, স্থপতি, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা, লেখক, শিক্ষাবিদসহ সর্বস্তরের সুশীল সমাজের সদস্যবর্গ চুপ করে থাকতে পারেননি। তাঁরা পরিকল্পিত চট্টগ্রাম ফোরাম নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে পরিকল্পিত চট্টগ্রাম গড়ে তোলার জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সভা, গোলটেবিল আলোচনা এবং মিছিল করে নগরবাসীকে সচেতন করার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ফারুক-ই-আজম এই ফোরামের সদস্য হয়ে সমস্ত কর্মকাÐের সঙ্গে নিজেকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছিলেন। এক সময় চট্টগ্রাম শহরে যত্রতত্র বাড়িঘর, কমিউনিটি সেন্টার, কিন্ডারগার্টের এবং মার্কেট নির্মাণের হুজুগ পড়ে গিয়েছিলো। শৈল শহর চট্টগ্রামে পাহাড় কেটে পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি এবং খাল, নালা, পুকুর, দিঘি ভরাট করে পানি নিষ্কাশনের পথ রুদ্ধ করে দেওয়ার ফলে শহরে জলাবদ্ধতা দেখা দিলে প্রকৌশলী, স্থপতি, পেশাজীবী এবং নাগরিক সংগঠনগুলো সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো। এসময় একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো, যার পুরোভাগে ছিলেন প্রকৌশলী এবিএমএ বাসেত, প্রকৌশলী সুভাষ বড়–য়া, স্থপতি জেরিনা হোসেন, প্রকৌশলী আলী আশরাফ, প্রকৌশলী দেলোয়ার মজুমদার, স্থপতি বিধান বড়–য়া, ইতিহাসবিদ শামসুল হুসাইন, ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক, সাংবাদিক আবুল মোমেন, এডভোকেট রাণা দাশগুপ্ত।
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবাহী দলিল, নানা উপকরণ সংরক্ষণের জন্য একটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি ইতিহাসবিদ শামসুল হুসাইন, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ড. মাহবুবুল হক, সাংবাদিক আবুল মোমেন, রুশো মাহমুদ ও রইসুল হক বাহার, মুক্তিযোদ্ধা বালাগাত উল্লাহ, সৈয়দ আবুল বশরকে নিয়ে।
বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক ই আজম বীর প্রতীক ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত ফরহাদাবাদ গ্রামের গুল মোহাম্মদ চৌধুরী বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার নিম্নবিত্ত এক কৃষক পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফারুক-ই-আজম, তাঁর পিতা রাওয়ালপিন্ডিতে ব্রিটিশ ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে মেডিকেল বিভাগে কোন কাজ করতেন। ভারত বিভক্তির সময় বাড়ি এসে তিনি আর পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মস্থলে যোগদান করেননি। তিনি স্থানীয়ভাবে মানুষকে চিকিৎসাসেবা দিয়ে কিছু উপার্জন করতেন, আর অনিয়মিতভাবে সেনা কল্যাণ সংস্থার কিছু অনুদান পেতেন। সেসবের সঙ্গে স্বল্প কৃষি আয়ে আট সন্তানের বোঝা টেনে বড় ছেলে ফারুক-ই-আজমকে পড়ানোর সাধ্য কিংবা ইচ্ছা তাঁর ছিল না। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফারুক-ই-আজম হাটহাজারীর কাটিরহাট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাস করেন। এরপর চরম দারিদ্র্যের কারণে ভাগ্যান্বেষণে তিনি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মাত্র ৫০ টাকা নিয়ে খুলনায় চলে যান। পড়াশোনা চালানো আর সম্ভব হয়নি।
১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ২৭ মার্চ যুদ্ধ করতে চট্টগ্রাম চলে আসেন। ২৮ জনের একটি দল সাথে তিনি মে মাসের ৫ তারিখ ফটিকছড়ি, কাঞ্চননগর, রামগড় হয়ে ভারতে যাওয়ার জন্য পরিবারের অলক্ষে ভোররাতে ঘর থেকে বের হন। সেদিন ওই দলে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে যাদের নাম তাঁর মনে আছে তারা হলেন: রফিকুল আলম চৌধুরী, মোহাম্মদ মুসা চৌধুরী, মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন, শাহ আলম, আহাম্মদ ছাফা, আবদুর নবী, মোহাম্মদ আলী, মাহাবুবুল আলম, কাজী মোহাম্মদ মহসিন, এবিএম নুরুল আনোয়ার, আবুল বশর, আবুল হাশেম, মোহাম্মদ হোসেন ফরিদ, ফারুক আহাম্মদ, সিরাজুল হক, খাইরুল বশর, এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী (সম্ভবত নগর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সিটি মেয়র; তিনি জেলে ছিলেন, পাগলের অভিনয় করে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ভারতে যাওয়ার পথে কাটিরহাটের উক্ত দলের সহযাত্রী হয়েছিলেন), মাহবুবুল হক চৌধুরী, নুরুল আবছার চৌধুরী প্রমুখ। এর মধ্যে শুধু মহিউদ্দিন চৌধুরী ছিলেন রাউজানের অধিবাসী, অন্যরা সবাই হাটহাজারী-ফটিকছড়ির বাসিন্দা। তাঁরা ফেনী নদীর পাড়ে পৌঁছে নৌকায় করে নদী পার হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাব্রæমে যান। সেখান থেকে হরিণা ক্যাম্পে যান। সেখানে নৌযুদ্ধের জন্য কমান্ডো নেয়ার হচ্ছে দেখে ফারকও ইন্টারভিউ দেন এবং নির্বাচিত হয়ে যান। জানানো হলো তাঁদেরকে নৌ যুদ্ধের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদেরকে দেশের অভ্যন্তরে নদী-বন্দরে যুদ্ধ করতে পাঠানো হবে। ভারতীয় নৌবাহিনী তাদের প্রশিক্ষণ দেবে।
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রথমে সবার নামধাম, চেহারার সামনে এবং দুপাশের ছবি ধারণ করা হলো। ভারতীয় নৌবাহিনীর কমান্ডার সামন্ত এ ক্যাম্পের ইনচার্জ। তার অধীন ভারতীয় কমান্ডোরা লে. কমান্ডার জি. মার্টিসের নেতৃত্বে ভাগীরথী নদীক‚লের গোপন সুরক্ষিত ক্যাম্পে তাদের প্রশিক্ষণ দেবেন। প্রশিক্ষণের সুবিধার জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ২৯৬ জনকে ১০টি পৃথক দলে বিভক্ত করা হলো। এ থেকে জে পর্যন্ত প্রতি দলে ৩০ জন করে ভাগ করা হয়। তাদের প্রত্যেকের আলাদা নম্বরও দেওয়া হয়। ফারুকের গ্রæপ সর্বশেষ গ্রæপ, নম্বর ছিল ০২৮১।
জুন মাসের ১ তারিখ থেকে তাদের কঠোর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি দুভাগে ভাগ করে খুবই নিবিড় কঠোরতায় কার্যকর করা হতো। ভাগীরথী নদীতে তাদের প্রশিক্ষণ হয়। প্রশিক্ষণস্থলে এসে সব গ্রæপ একসঙ্গে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে প্রথমে কোরাসে ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ গাইতো।
প্রশিক্ষণ শেষ হলে আগস্ট মাসের ১ তারিখে পূর্ব পাকিস্তানের সব নদী ও সমুদ্রবন্দরের জন্য কমান্ডো দল বাছাই করা হলো। ফারুক-ই-আজম চট্টগ্রামের জন্য বাছাই করা ৬০ জনের দলে অন্তর্ভুক্ত হন। দলের অধিনায়ক মনোনীত হলেন সাবমেরিনার এ ডবিøউ চৌধুরী (আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী বীর উত্তম, বীর বিক্রম)। তিনি ফ্রান্স থেকে পালিয়ে আসা বাঙালি নাবিকদের একজন ছিলেন। তার ডেপুটি হলেন শাহ আলম (শাহ আলম বীর উত্তম), তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। সার্বিক সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্য চট্টগ্রামের দলকে ২০ জন করে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। বিভক্ত ২০ জনের একটি দলে শাহ আলম অধিনায়ক এবং ফারুক-ই-আজম তার ডেপুটির দায়িত্ব পান। এভাবে মোংলা, খুলনা, বাহাদুরাবাদ, দাউদকান্দি, চাঁদপুরসহ সব গুরুত্বপূর্ণ নদী ও সমুদ্রবন্দরের জন্য দল ঠিক করা হয়। উপস্থিত কমান্ডোদের মধ্যে প্রায় ২০০ জন প্রথম অভিযানের জন্য মনোনীত হন। প্রধান প্রশিক্ষক লে. কমান্ডার জর্জ মার্টিস আবেগঘন বক্তব্য দিয়ে তাদের নিরাপত্তা ও সাফল্য কামনা করে বিদায় জানান।
আগস্টের ১১ তারিখে তাঁদেরকে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন শ্রীনগর সাবসেক্টর ক্যাম্পে নেয়া হলো। ১ নম্বর সেক্টরের অধীন এই সাবসেক্টরের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট মাহফুজুর রহমান, ওখানে সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন রফিক (মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম) ও ভারতীয় উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং উপস্থিত থেকে সবকিছু তদারক করেন। তাদের অস্ত্রশস্ত্র বণ্টন করে দেয়া হলো। প্রত্যেকে একটি লিমপেট মাইন, এক জোড়া ফিন্স, একটি কমান্ডো ড্যাগার, কিছু প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ এবং কাউকে কাউকে ৯এমএম কারবাইন ও গ্রেনেড দেয়া হয়। রাত প্রায় ১০টায় সীমান্ত অতিক্রম করে তারা দেশে ঢোকেন। গাইড ছিল সীতাকুÐের এক শ্রমিক নেতা নূর আহমদ। নূর আহমদের সাথে মিরসরাই পৌঁছার পর মাঝপথ থেকে তাঁরা বদিউল আলমের (স্বাধীনতার পর লালখান বাজার ওয়ার্ডের পৌর কমিশনার, আওয়ামী লীগ নেতা) সাথে সমিতির হাটে আসেন। সেখারন থেকে যার যার অস্ত্র ও বিস্ফোরক কাঁধে-পিঠে নিয়ে তার পিছনে পিছনে আবার যাত্রা করলেন। বেলা ১১টায় লুঙ্গি-শার্ট পরে বাসের ভাড়া নিয়ে গ্রামের মানুষের সঙ্গে গ্রাম্য মেঠো পথে হেঁটে তারা ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডে উঠেন। রাস্তার ওপর একটি ছোট বাজারমতো জায়গায় বাস স্টেশনে এসে অপেক্ষার সময় আরও একজন কমান্ডোকে সঙ্গে করে মাজহার উল্লাহও আসেন। তিনি আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরীর প্রথম গ্রæপ ২০ জনের উপনেতা। কিছুক্ষণ পর চট্টগ্রামের বাস আসলে তারা আগে-পিছে উঠে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসেন কন্ডাক্টরকে চট্টগ্রাম শহরের নিউমার্কেট পর্যন্ত ভাড়া দিয়ে। অবশেষে নিরাপদে দুপুরে এসে নিউমার্কেটের পাশে নামলেন। শহরের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। গাড়ি-রিকশা-ট্যাক্সি চলছে। লোকজনের চলাফেরাও প্রচুর। জনারণ্যে মিশে তারা চারজন একসঙ্গে বদিউল আলমের পরামর্শমতো নিউমার্কেটের দক্ষিণ পাশে আলকরণ গলির মুখে মতিন টেইলার্সে যান। ছোট দোকানটিতে একটা লোক টেবিলের ওপর কাপড় কাটছিল। তাঁরা তাকে বললেন, আমরা মিরসরাই থেকে এসেছি। তাদের বয়সি দুটি ছেলে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। এসে হাত বাড়িয়ে বলল, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি রিকশা ডেকে তারা তাদের পাঠানটুলী চৌমুহনীর পশ্চিমে রাস্তা থেকে বেশ ভেতরে হাজিপাড়ায় নিয়ে যায়। এলাকাটি তেমন উন্নত ছিল না। ইতস্তত দু-একটি পাকা দালান আর অধিকাংশই টিনের ছাউনির কাঁচাঘর। এমনি একটি বেড়ার ঘরে তাদের বিশ্রাম নিতে বলে তারা অন্য কমান্ডোদের আনতে চলে গেল। যাওয়ার সময় তাদের খাবার ঘরে পাঠাচ্ছে বলে বাইরে বেরোতে নিষেধ করল। ঘরে দুটি চৌকিতে বিছানো পাটির বিছানায় বসে গল্প করার সময় দুটি ছেলে খাবার নিয়ে এলো। ঘরের পাশের চাপকলে হাত-মুখ ধুয়ে মাছ-তরকারি দিয়ে তারা ভাত খান। সন্ধ্যায় তরুণ সংগঠক আবু সাঈদ সর্দার শেলটারে আসেন। তিনি জানান, তাদের সব কমান্ডো নিরাপদে শহরে এসে গেছে এবং বিভিন্ন শেলটারে তাদের রাখা হয়েছে। তার সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে ফারুক প্রথমে নাপিতের দোকানে ঢুকে চুল কাটান। তারপর তিনি রাস্তার পাশের একটি হোটেলে নিয়ে যান। অনেক দিন তাদের গরুর মাংস খাওয়া হয়নি, সবাই মিলে পেট ভরে গরুর মাংস দিয়ে রাতের খাবার যান। পরদিন ছিল ১৪ আগস্ট, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। সে কারণে রাস্তায় পাকিস্তানি সেনা-পুলিশের নিরাপত্তা টহল বেশি থাকবে। তাদের সাবধান করে শেলটারে পৌঁছে দিয়ে আবু সাইদ সর্দার চলে যান। রাতে মশার উপদ্রব সত্তে¡ও ভালো ঘুম হলো। সকালে কোনো হোটেল থেকে তাদের নাশতা দেওয়া হয়। বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় সংগঠকের সঙ্গে শাহ আলম আসেন। তার সঙ্গে আবু সাঈদ সর্দারের ছোট ভাই আবু ছিদ্দিক সর্দার। তিনজন মিলে বিভিন্ন শেলটারে তাদের গ্রæপের ছেলেদের খোঁজে বের হন। সব শেলটার ঘুরে দেখেন তিনজন কমান্ডোকে পাওয়া গেল না। তার মধ্যে সীতাকুÐের সিরাজ-উল-দৌলা, মিরসরাইয়ের বলিষ্ঠ গড়নের রেজা এবং ফটিকছড়ির আবুল বশর-তিনজনই ফারুকের গ্রæপের। বিকেলে ফারুক স্থানীয় সংগঠক আলাউদ্দিন ও আবু সাঈদ সর্দার তাদের নেতার সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে গেলেন। লুঙ্গিপরা হ্যাংলা-পাতলা মতো এক তরুণ তাদের শেলটারের মতোই আরেকটি বাঁশের ঘরে চৌকিতে বসা ছিলেন। তিনি মৌলবী সৈয়দ (চট্টগ্রাম শহরে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠক এবং তিনিই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেন)। তাদের কমান্ডো অভিযানের স্থানীয় সাহায্য-সহযোগিতার সবকিছু তিনিই দেখাশোনা করছেন। কমান্ডোদের ঘরের বাইরে অপ্রয়োজনে চলাফেরা না করার পরামর্শ দিলেন তিনি। ফারুকের চেয়ে কিছুটা বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও বন্ধুর মতো ব্যবহার করলেন। কোনো অসুবিধা হলে তাকে জানাতে বললেন। তাদের অস্ত্র দেখতে কিশোর সংগঠক আবু ছিদ্দিক সর্দারের সঙ্গে জালালউদ্দিন (আগ্রাবাদের সাবেক কমিশনার ও আওয়ামী লীগ নেতা), আলাউদ্দিনদের (জালালউদ্দিনের ভাই) বাড়িতে যান। তাদের টিনের ছাউনি কাচারিঘরের ছাদে মাইন, ফিন্স ও অন্যান্য অস্ত্র চটের বস্তায় লুকানো হয়েছে। আবু ছিদ্দিক সর্দার নামে কৈশোর উত্তীর্ণ যুব সংগঠকের উৎসাহ ও সাহস অভিভূত হওয়ার মতো। সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আরও দু-তিনজন কমান্ডো মিলে রাস্তার পাশে তাদের পরিচিত হোটেলে গিয়ে গরুর মাংস ভাত খান। হোটেলের কাছেই তাদের শেলটার। অন্যদের থেকে বিদায় নিয়ে ফারুক ও মাজহার উল্লাহ ঘরে এসে শুয়ে পড়েন।
১৫ আগস্ট সকাল ১০টার দিকে লম্বা ছিপছিপে এক সংগঠকের সঙ্গে শাহ আলম এসে জানান, রাতেই অভিযান হবে। কমান্ডোদের পাকিস্তান বাজার ঘাট (বর্তমানে বাংলা বাজার ঘাট) দিয়ে একজন-দুজন করে সাধারণ বেশে কর্ণফুলীর ওপারে যেতে হবে। তার সঙ্গে আসা কর্ণফুলীর ওপারের চরলক্ষ্যার সংগঠক নিজেকে ইউনুস নামে পরিচয় দেন। তিনি বলেন, ঘাটের দুদিকেই স্থানীয় সংগঠকরা তাদের পারাপারের দায়িত্বে থাকবে। তা ছাড়া, নিজেদের সাম্পানও থাকবে। তারা নির্দিষ্ট স্থানে কমান্ডোদের পৌঁছে দেবে। ফারুক-ই-আজমরা একসঙ্গে জালাল উদ্দিনের (পরবর্তীকালে পৌর কমিশনার, প্রয়াত) বাড়িতে গিয়ে অভিযানস্থলে পৌঁছানোর জন্য মাইন, ফিন্স, কমান্ডো ড্যাগার বুঝিয়ে দেন ইউনুসকে। তখনো কমান্ডোদের তৃতীয় দলটি শহরে পৌঁছায়নি। সেই সঙ্গে তাদের তিনজনও আসেনি। শাহ আলম বললেন, তাদের ছাড়াই অভিযান হবে। সব কমান্ডোকে সন্ধ্যার আগে সংগঠকদের সঙ্গে অভিযানে পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে শাহ আলম কাকলীতে ফিরে যান। দুপুরে খাবারের পর থেকে হাজিপাড়া পান্নাপাড়া এলাকার সংগঠকরা বিভিন্ন শেলটার থেকে কমান্ডোদের নির্বিঘেœ পাকিস্তান বাজার ঘাটে পৌঁছে দেন। শেষ বিকেলে আবু ছিদ্দিকের সঙ্গে ফারুক ও মাজহার উল্লাহ পাকিস্তান বাজার ঘাটে গেলে ইশারায় ডেকে এক সংগঠক যাত্রীপূর্ণ খেয়া সাম্পানে তাদের তুলে দেন। নদী পার হয়ে কর্ণফুলীর একটি নির্জন চরে একটি মহিষের বাতান ঘরে আশ্রয় নেন। ইতোমধ্যে প্রায় সব কমান্ডোই পৌঁছে গেছে। শুধু কমান্ডাররাই আসেননি। তারা জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকেন চুপচাপ। সন্ধ্যার পর মাটির সানকি ও সবজি আনাজের আড়ালে লাইয়ে লাইয়ে তাদের অস্ত্রও পৌঁছে গেল। রাত ৮টার দিকে আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী, শাহ আলম অন্য কয়েকজন সংগঠকের সঙ্গে বাতানে আসেন। অভিযানের কমান্ডার আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী তাদের উদ্দেশে বললেন, রাতেই অভিযান করতে হবে। যার জন্য আমরা দুই মাস প্রশিক্ষণ নিয়েছি তার সঙ্গে রাখা একটি ট্রানজিস্টর দেখিয়ে বললেন, এই অভিযান পাকিস্তানের সব নদী ও সমুদ্রবন্দরে একসঙ্গে পরিচালিত হবে। কলকাতায় ইন্ডিয়ান ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টার পোর্ট উইলিয়ামে আসার সময় তাদের এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অভিযান সমন্বয় করার জন্য আকাশবাণী কলকাতা বেতার থেকে সকালের খবর পড়ার পরপরই দুদিন দুটি গান বাজানো হবে। প্রথম গান ‘আমি তোমায় যত শুনিয়ে ছিলাম গান’ পরশু রাতে বাজানো হয়েছে। সংকেত ছিল, এ গান শোনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযানস্থলে পৌঁছাতে হবে। দ্বিতীয়টি আজ সকালে আকাশবাণীর খবরের পর বাজানো হয়েছে ‘আমার পুতুল আজকে প্রথম যাবে শ্বশুর বাড়ি’। এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত আক্রমণের সংকেত অর্থাৎ রাতেই অভিযান সম্পন্ন করতে হবে। তাই তাদের এ রেডিওটি দিয়েছিল। তিনি দেশের স্বাধীনতায় এই অভিযানের সংক্ষিপ্ত গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলেন। এরপর আগরতলা থেকে সঙ্গে আনা সক্কর প্যাড়ার অবশিষ্ট দিয়ে সবাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেন। রাত ১১টায় সবাই নদীর পাড়ে উপস্থিত হন। ফারুক পরণের কাপড় খুলে সংগঠকের হাতে দেন। এখন তাদের পরণে সাঁতারের জাঙিয়া, তাতে গোঁজা কমান্ডো ড্যাগার, পায়ে ফিন্স (এক প্রকার সাঁতারের জুতা), হাতে ১টি লিমপেট মাইন ও গামছা। নদীর ওপারের জেটি, জাহাজ এবং নদীর মধ্যে নোঙর করা জাহাজের আলোয় তাদের আবছা দেখা যাচ্ছিল। তারই মধ্যে প্রতি জাহাজের জন্য তিনজন কমান্ডোকে টার্গেট দেওয়া হলো। একইভাবে জেটি পন্টুন এবং ভাসমান বার্জকেও ডোবাতে হবে। যদি পাকিস্তানিরা গানবোট নিয়ে সক্রিয় হয়, তবে ক‚লে হাবিলদার শমশু রকেট লঞ্চার থেকে গোলাবর্ষণ করে তাদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করবে। শমশুকে শ্রীনগর সাব-সেক্টর থেকে পাঁচটি গোলাসহ তাদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে এ কাজের জন্য। আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী জাহাজে মাইন লাগিয়ে সব কমান্ডোকে তার অবস্থানে ফেরত আসার নির্দেশ দিয়ে ৩৭ জনকে অভিযানে পাঠালেন। তারা পানির ধার বরাবর ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে যার যার নির্ধারিত টার্গেট ধ্বংসের জন্য সাথিদের নিয়ে পানিতে নামেন। নদীতে তখন জোয়ারও নয় ভাটাও নয়। জোয়ার-ভাটার মাঝামাঝি সময় পানি অনেকটা স্থির। গামছা দিয়ে লিমপেট মাইনটি বুকের ওপর বেঁধে তারা চিত হয়ে সাঁতার শুরু করেন। নিঃশব্দে সাঁতার কেটে ওপারে জেটিতে পৌঁছে সংলগ্ন একটি বড় বার্জ পেলেন। জেটিতে উজ্জ্বল আলো থাকলেও কোনো পাহারাদার ছিল না। ডুব দিয়ে জাহাজের নিচের দিকে মাইন লাগানোর নির্দেশ ও প্রশিক্ষণ ছিল; কিন্তু এই সময় ভয়জনিত অতি উত্তেজনায় অতি দ্রæত শ্বাস নিতে হচ্ছিল বিধায় ডুব দেওয়া সম্ভব হলো না। ফারুক গামছা খুলে মাইনটি হাতের নাগালের মধ্যে বার্জের গায়ে দ্রæত লাগিয়ে দেন। মাইনের তলায় লাগানো শক্তিশালী চুম্বক জাহাজে আটকে গেল। এবার দ্রæত প্লাস্টিকের নিরাপত্তা ক্যাপটি খুলে নেন। বিস্ফোরণের প্রক্রিয়া শুরু হলো। এখন পালানোর জন্য মাত্র আধঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে। যত দ্রæত সম্ভব নিঃশব্দে সাঁতরে ওপারে ফিরে আসেন। নির্ধারিত জায়গায় সংগঠকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী অভিযান পরিচালনা করছিলেন। তার কাছে ফিরে পানি থেকে ওঠার সময় ফারুক পায়ের ফিন্স জোড়া নদীতে ফেলে দেন। ইতোমধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। নদীতে বা জেটিতে পাকিস্তানিদের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না। কমান্ডোরা একে একে সবাই উঠে এলে কালবিলম্ব না করে সাঁতারের জাঙিয়া পরা অবস্থায় নদীর পাড় থেকে পালাতে থাকেন। কৃষকের সদ্য রোপা ধানখেত আর আলপথ মাড়িয়ে সংগঠকদের পিছনে পিছনে সবাই বৃষ্টি মাথায় করে দৌড়াতে দৌড়াতে শুনতে পান, দিগন্ত বিদীর্ণ শব্দ করে মাইনগুলো ফাটতে শুরু করেছে। মুহুর্মুহু বিস্ফোরণে চট্টগ্রাম বন্দর ও আশপাশ কেঁপে কেঁপে উঠছিল। তারা কেবল উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিলেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। ভোরের আজানের সময় বহু দূরে এক গৃহস্থবাড়ির ছোট পুকুরসংলগ্ন জীর্ণ কাচারিঘরে এসে তারা থামেন। পুকুরের ঘাটে ময়লা-কাদা পরিষ্কার করে আধা ভেজা কাপড়ের পোঁটলা থেকে নিজের লুঙ্গি-জামা খুঁজে নিয়ে পরে নিলেন। ওখানে জড়ো করা খড়ের গাদায় অনেকে এলিয়ে পড়েন। ধানি জমির আলপথে ছুটতে গিয়ে হাবিলদার শমশুর পায়ে খেজুর কাঁটা বিঁধে তিনি কাহিল হয়ে কাতরাচ্ছিলেন। সারা পথ তাঁকে প্রায় বহন করে আনতে হয়েছে। সকালে গৃহস্থবাড়ি থেকে ধারালো রেজর বেøড চেয়ে নিয়ে তা আগুনে পুড়িয়ে শাহ্ আলম শমশুর পা কেটে কাঁটা বের করেন। যুদ্ধের সময় শাহ আলম চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। কাটা ঘায়ে কাঁচা হলুদ বেটে মলম লাগিয়ে পট্টি বেঁধে দিলে শমশু কিছুটা স্বস্তি পান। তাদের অবস্থানের ওপর পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান চক্কর দিয়ে যায়। অভিযানের সাফল্যের খুশি ও ধরা পড়ার আতঙ্কে তারা বিচলিত হন। সকাল ৮টার দিকে সংগঠক ও গাইডের পেছনে পেছনে কমান্ডোরা কেউ লুঙ্গি, কেউ প্যান্ট পরে একজন-দু’জন করে হাজি অছি মিঞা চৌধুরী ঘাট, ব্রিজঘাট দিয়ে সাম্পানে সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে মিশে কর্ণফুলী পেরিয়ে শহরে চলে আসেন। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেদিনই ফারুক রাতের খাবারের পর নির্ভরযোগ্য গাইড নুর আহমদের সঙ্গে শ্রীনগর সাব-সেক্টরে চলে যান।
১৫ আগস্টের পরে ফারুক আরো তিনটি অপারেশন করেন। অপারেশন জ্যাকপট শেষ করে হরিণা ফিরে যাওয়ার পর তাঁকে কর্ণফুলীর নাব্যতা ব্যাহত করা এবং বন্দরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য একটি অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হয়। ৯জন কমান্ডো নির্বাচন করা হয়। মাজহারউল্লাহকে অপারেশনের কমান্ডার এবং ফারুক-ই-আজমকে ডেপুটি কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। ৯জন কমান্ডো হচ্ছেন-আমির হোসেন, শফিকুল নূর মওলানা, নুরুল হক, রশিদ, জাহাঙ্গীর আলম মুহিবুল্লাহ, জয়নাল আবেদিন কাজল, আবু বকর সিদ্দিক। তিনজন কমান্ডোকে একটি করে জাহাজ ধ্বংস করার দায়িত্ব দিয়ে ৯জনকে তিনটি জাহাজ ডুবানোর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মাজহারউল্লাহ খেজুর কাঁটা ফ‚টে আহত হওয়ায় যেতে না পারায় ফারুকই অধিনায়ক হন। পতেঙ্গা ১৫নং ঘাট দিয়ে কর্ণফুলী পার হয়ে সবাইকে নিয়ে মোহছেন আউলিয়ার দরগায় যান। রাত ১টায় কমান্ডোরা সাগরে নেমে গেলে চরে পাহারায় থাকেন লোকমান গনি চৌধুরী (গ্রæপ কমান্ডার-শিকলবাহা বাড়ি, কমার্স কলেজের ছাত্র), মোহরার রফিক, সাতকানিয়ার আলম, মাদারবাড়ির নুর মোহাম্মদ, রাবেয়া ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শাহজাহান। চিংড়ির ঝাঁকে পড়ে, কেউ দিগভ্রান্ত হয়ে, কেউ সহযোদ্ধা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্দিষ্ট টার্গেটে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়ে ভোর ৪টায় মুমূর্ষ অবস্থায় সাগরে সবকিছু ফেলে ৫জন কমান্ডো তীরে উঠে আসে। তারা হলেনÑজয়নাল আবেদিন কাজল, আবু বকর ছিদ্দিক, জাহাঙ্গীর আলম, আবদুর রশিদ ও মুহিবুল্লাহ। সুফিকুর নুর মওলা, আমির হোসেন, নুরুন হক, মোহাম্মদ হোসেন ফরিদ। ফরিদ ধরা পড়ে। নুর মোহাম্মদ (স্টীল মিলের শ্রমিক নেতা, স্বাধীনতার পর প্রথমে জাসদ ও পরে বাসসের নেতা), নুরুল হক, ইউনুস (লক্ষ্যারচর) এই অপারেশনে সহযোগিতা করেন।
আবার তিনটি জাহাজ ডুবানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই তিনটি জাহাজের ২টি হলোÑআল মানা এবং অ্যাভলুস। অভিযানের জন্য টিম গঠন করা হয় মনোজ কুমার দত্ত, আবু মুসা চৌধুরী, নোমান ও শাহজাহানকে নিয়ে। সন্ধ্যায় মাইন লাগিয়ে তাদের নদীর ওপারে যাওয়ার কথা। রাত ৯.৩০টায় মাইন ফাটে। অ্যাভলুস ডুবে যায়।
অক্টোবরে আরেকটি অভিযানের পরিকল্পানা নেওয়া হয়। সল্টগোলা খাল দিয়ে সে অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১০ অক্টোবর ২জন কমান্ডো আবু তাহের, সাইদুর রহমান অপারেশনের জন্য হালিশহর ঈশান মিস্ত্রির হাটে কালু সওদাগরের ৩ তলা বাড়িতে অবসর নেন। সেখানে ছোট খালে নেমে তারা সল্টগোলা খাল দিয়ে একটি রেললাইন ও বড় রাস্তার নিচ দিয়ে কর্ণফুলীতে নামেন। রাত ১০টায় মনু ফিরে আসেন আস্কর খাঁর দীঘির পাড়ের সেল্টারে। ৩নং জেটিতে এমডি রশিদ নামের টাগ জাহাজ ও জেসি পন্টুনে মাইন লাগাতে পাহারাদাররা দেখে ফেলায় তাঁরা চলে আসেন । তবে কর্ণফুলীতে একটি বড় জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
এই অভিযানের পর শীতললক্ষ্যা নদীতে একটি অপারেশনের টার্গেট দেওয়া হয় ফারুক-ই-আজমকে। অভিযানের জন্য ৮জন কমান্ডো নির্বাচিত হন, তাঁরা হলেন আবু মুসা চৌধুরী, আবু তাহের, সাইদুল হক মনু, মনোজ, মোহাম্মদ নুরুল গণি, শ্যামল কর্মকার, জসিমউদ্দিন ও আবদুর রহিম। তাঁরা মিনি লায়ন জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটান।
ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচিত চট্টগ্রাম জেলা ইউনিটের কমান্ডার ও কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের ডেপুটি সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন।
নোবেলজয়ী ড. ইউনূস সুহৃদের সাধারণ সম্পাদক ও সামাজিক ব্যবসা কেন্দ্র চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে সামাজিক ব্যবসায় তরুণ উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন।
ফারুক-ই-আজম চার কন্যা সন্তানের জনক, স্ত্রী শামীমা ফারুক।